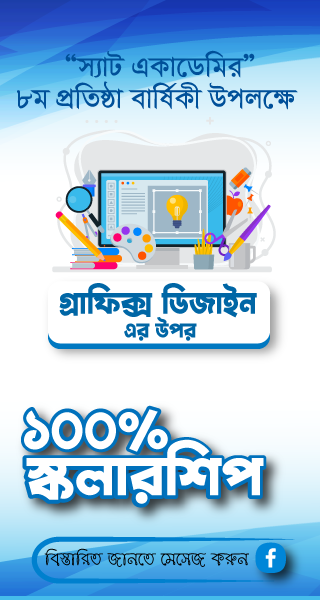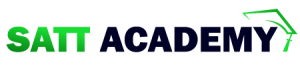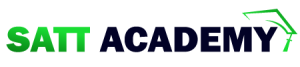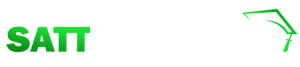একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শিশুটির বড় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে কাল হিসেবে ধরা হয়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শৈশবকাল। শৈশবকালে ছেলে বা মেয়ে সকলকে শিশু বলা হয়। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বলি বাল্যকাল। বাল্যকালে শিশু মেয়ে হলে বালিকা এবং ছেলে হলে বালক বলা হয়। দশ থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে তাদের শরীর যথাক্রমে পুরুষের বা নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে বাল্যকাল ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়। একটি শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, তার জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই তার সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি জড়িত। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য কী এবং এটা রক্ষা করার বিষয়ে সবারই জানা প্রয়োজন।
এ অধ্যায় শেষে আমরা-
- বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সময় কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন প্রকার মানসিক চাপ মোকাবিলার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অটিজম সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও বর্ণনা করতে পারব।
মানুষের জীবনে বয়সের ভিত্তিতে অনেকগুলো পর্যায় আসে। যেমন— শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল, ছয় থেকে দশ বছর বাল্যকাল, দশ থেকে ঊনিশ বছর কৈশোরকাল বলা হয়। কৈশোরকালে একটি ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকালে কিশোর বা কিশোরীরা শারীরিকভাবে পুরুষ বা নারীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কৈশোরকালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল আগে শুরু হয়। মেয়েদের আট থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু দশ থেকে পনেরো বছর বয়সে। কারো কারো ক্ষেত্রে এর আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে।
বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। বয়ঃসন্ধিকালে যে সব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত ৩ প্রকার ।
১. শারীরিক ২. মানসিক ৩. আচরণিক
বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন
কিশোরদের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে-
ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
খ. শরীরে দৃঢ়তা আসে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
গ. এ বয়সে দাড়ি গোঁফ উঠে।
ঘ. স্বরভঙ্গ হয় ও গলার স্বর মোটা হয় ।
ঙ. বীর্যপাত হয়।
কিশোরীদের পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ-
ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
খ. শরীর ভারী হয়, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হয় ।
গ. ঋতুস্রাব শুরু হয়।
বয়ঃসন্ধিকালে সবার ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। যেমন কিশোরীদের ক্ষেত্রে কারো আগে বা পরে ঋতুস্রাব শুরু হতে পারে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে সকলের উচ্চতা একইভাবে নাও বাড়তে পারে।
বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা রকম মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এইসব পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব মানসিক পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায়—
ক. অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে।
খ. শারীরিক পরিবর্তনের ফলে চলাফেরায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে।
গ. স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে।
ঘ. নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়
ঙ. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।
চ. ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।
ছ. মানসিক পরিপক্বতার পর্যায় শুরু হয়।
আচরণিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই-
ক. প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে।
খ. বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।
গ. প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।
ঘ. দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
| কাজ-১ : শিক্ষকের নির্দেশ মতো ৫/৭ জনের দল গঠন কর। তোমার সহপাঠী/সমবয়সীদের কথা ভাব। প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন পরিবর্তনগুলো দিয়ে নীচের ছক দুইটি পূরণ কর। এর শিরোনাম দাও “সাধারণ পরিবর্তন”। এরপর অবশিষ্ট পরিবর্তনগুলো দিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর। এর শিরোনাম হবে “অন্যান্য পরিবর্তন”। এটা হবে দলগত কাজ । |
| বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণ পরিবর্তন | |
| শারীরিক পরিবর্তন | মানসিক পরিবর্তন |
|
১ ২ ৩ ৪ |
১ ২ ৩ ৪ |
| বয়ঃসন্ধিকালে অন্যান্য পরিবর্তন | |
|
১ ২ ৩ ৪ |
১ ২ ৩ ৪ |
আমরা পূর্বেই জেনেছি যে সাধারণত ছেলে-মেয়েদের ১০-১৯ বছর বয়সের সময় কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাওয়া, স্থান, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও মানের তারতম্যের কারণে এক একজনের বয়ঃসন্ধিকালের শুরুর সময়ে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। হরমোন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যার কারণে বয়ঃসন্ধিকালের পরিববর্তনগুলো ঘটে। মেয়েদের শরীরে ও মনে বিভিন্ন পরিবর্তনে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামক দুটি হরমোন কাজ করে আর ছেলেদের যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ ঘটে তা টেস্টোস্টেরন নামক হরমোনের কারণে হয়।
বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ : ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ পরিবর্তনগুলো অনেকটা আকস্মিকভাবে শুরু হয়। এর সাথে পরিচিত না থাকার কারণে তারা আতংকিত হয়ে পড়ে এবং অপরাধবোধে ভোগে। এসময় তাদের বুঝিয়ে বললে তারা আতংকিত হবে না এবং তাদের মনে কোনো অপরাধবোধ কাজ করবে না। এ ধরনের অপরাধবোধ ও মানসিক দুশ্চিন্তা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে ছেলেমেয়েদের মনে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করে। তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং অনেক সময় পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে এবং এ সম্বন্ধে করণীয় বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকলে, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। ফলে তারা বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় না এবং সম্ভাব্য রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন ঘটলে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে। ফলে সংকোচ কেটে যাবে এবং একা থাকার প্রবণতা কমে যাবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগিক পরিবর্তনও ঘটে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সাথে মা বাবা ও অভিভাবকদের বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্য সব ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান ও সাহস যোগাতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তাদের নিজেদেরকেও সচেষ্ট থাকতে হবে। তাদের প্রথম কাজ হবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। ভালো গল্পের বই পড়লে, সাথীদের সাথে খেলাধুলা করলে মনে প্রফুল্লতা আসবে এবং মানসিক চাপ সামলানো সম্ভব হবে।
| কাজ-১ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে তালিকার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক চাপ থেকে উত্তরণের কয়েকটি উপায় খাতায় লেখ। |
বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। সুস্থ দেহেই বাস করে সুন্দর মন। শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না। লেখাপড়া করতেও ইচ্ছে করে না। সেজন্য খাদ্য ও পুষ্টির দরকার। আবার যে কোনো খাবার খেলেই যে শরীর ভালো থাকবে তা নয়। কারণ সব ধরনের খাদ্যেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে না। সেজন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রতিদিনের খাবারে আমিষ, শর্করা, চর্বি বা তেল, , খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন ও পানি প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাওয়া যায়।
বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও সুষম খাদ্য : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজন খুব বেশি। কেননা এই সময়ে ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ বেড়ে উঠে এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তাদের প্রতিদিনই যথাযথ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকেরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ও পুষ্টি শুধুমাত্র দামি খাবার ও ফলমূলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। একটু সচেতন হলেই সহজপ্রাপ্য ও সুলভমূল্যের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়।
বয়স, দৈহিক গঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমাহারকে সুষম খাদ্য বলে। বয়সভেদে এই “প্রয়োজনীয় পরিমাণের” তারতম্য হতে পারে। যেমন ১৩/১৪ বছর বয়সের কোনো কিশোর বা কিশোরীর পুষ্টির প্রয়োজন একটি ৮/৯ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি। একই বয়সের মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর পুষ্টির প্রয়োজনে কোনো তারতম্য নেই। আবার দুজন একই বয়সের তরুণ বা তরুণী একজন বেশ দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান এবং অপরজন ছোটখাটো ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হলে, দৈহিক গঠনের কারণে প্রথমজনের প্রয়োজনীয় পুষ্টির তথা খাদ্যের পরিমাণ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশি হবে। দু'জন একই বয়সী ও একই রকম দৈহিক গঠনের পুরুষের মধ্যে যিনি বেশি দৈহিক পরিশ্রম করেন তার খাদ্যের প্রয়োজন বেশি হতে পারে। দু'জন সমবয়সী এবং একই রকম দৈহিক গঠন সম্পন্ন মেয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এভাবে বয়স, দৈহিকগঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয়। কারণ খাদ্যের ৬টি উপাদানের প্রত্যেকটিই বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে-মেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খুব প্রয়োজন। এগুলো দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। অন্যথায় যথাযথ পুষ্টির অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ছেলেমেয়েরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়।
|
কাজ-১ : কিশোর-কিশোরীদের জন্য সকল খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি দৈনিক সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি কর। এই তালিকায় সহজে পাওয়া যায় এবং দাম কম এমন খাদ্য অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। কাজ- ২ : বয়স, শরীরের গঠন ও কাজের ধরন অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ এবং পুষ্টিকর খাবার না খেলে কী কী অসুবিধা হয় তা লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর । |
প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। তাই প্রজনন বলতে সন্তান জন্মদানকে বোঝায়। পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য তথা সুস্থ প্রজনন তন্ত্রের উপর নির্ভর করে। তাই স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক ।
প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় : হরমোনজনিত কারণে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে ছেলে ও মেয়েরা ভয় পেয়ে যায় এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঋতুস্রাব ঘটলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত গোসল করা দরকার। এ সময়ে পুষ্টিকর খাবার ও প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রাথমিক অবস্থায় মা-বাবা, নিকটাত্মীয় বা স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময়ের মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি মনে রেখে ছেলে বা মেয়েদের সাথে বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। সহযোগিতামূলক আচরণ তাদের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে, তাদের মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে। প্রজনন স্বাস্থ্যের বড় ঝুঁকি হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হওয়া ও সন্তান ধারণ। এ কারণে রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়াও মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়সে বিয়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। নানা কারণে প্রজনন অঙ্গের রোগ দেখা দিতে পারে। প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে তা গোপন করা যাবে না। ডাক্তারের নির্দেশমতে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সংক্রামক রোগ এবং যৌনরোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যাবে ।
| কাজ-১ : প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন সেগুলো নিচের ছকে লেখ । করণীয় কাজ |
মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধু প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে বোঝায় না। এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সার্বিক সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।
প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান
১। বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি : বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
২। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ : মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করা যাবে না। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকে ।
৩। নিরাপদ মাতৃত্ব : নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে বোঝায় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের সুস্থতা বজায় রাখা। বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্ন হয় না। তিনি পর্যাপ্ত খাদ্য, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পান না। তাছাড়া অপরিণত বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ফলে মা ও শিশুর অসুস্থতাও ঘটে।
৪। শিশুর জন্য পূর্ব যত্ন : মায়ের গর্ভে সন্তান আসার পর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম, ঘুম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়।
৫। নবজাতকের পরিচর্যা : জন্মের পর থেকে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়। জন্মের পর
পরই শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো, টিকা প্রদান প্রভৃতি পরিচর্যামূলক সেবা শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৬। মা ও শিশুর পুষ্টি : আমাদের দেশে অধিকাংশ মা ও শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগেন বলেই শিশু অপুষ্টির শিকার হয়। ঘন ঘন গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব মা ও শিশুর অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ ৷
৭। প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সেবা ও রোগ প্রতিরোধ : প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ, যৌনরোগ, প্রজনন অঙ্গের ক্যান্সারসহ সব রকম রোগ। এসব রোগের সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে হবে।
গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধু মায়ের শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। যেমন- ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, বারবার প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি। পরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে শারীরিক ও মানসিক তেমন কোনো জটিলতা দেখা যায় না। গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও সেবা হচ্ছে-
ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।
খ. নিয়মিত গোসল করা।
গ. পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম ও ঘুম ।
ঘ. গর্ভধারণের প্রথম থেকেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা
ঙ. গর্ভকালীন সমস্যা মোকাবিলার জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা।
চ. প্রজননতন্ত্রের যে কোনো সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা ।
ছ. ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা। এছাড়া পড়াশুনাসহ বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত রাখা ইত্যাদি।
|
কাজ-১ : একজন গর্ভবতী মায়ের যে যে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি কর। কাজ-২ : গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরের যে সব অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায় তা ধারাবাহিকভাবে লেখ। |
দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। সুখ-দুঃখ হাসি কান্না আমাদের প্রতিদিনের ঘটনা। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মা-বাবা শিশুটির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা করতে থাকে। তাদের এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ। শিশুদের শারীরিক, মনো-সামাজিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যখন কোনো বাবা-মা বুঝতে পারে যে, তার শিশুটি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন আচরণ করছে অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করছে না বা বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে, তখন তাদের মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পরিবারটিতে নেমে আসে হতাশা। সন্তানের এই ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার জন্য মা-বাবাকে প্রথমত সংগ্রাম করতে হয় নিজের মনের সাথে। আবার সেই সাথে শিশুটির প্রতি সমাজের ও পরিবারের সদস্যদের বিরূপ বা নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মা-বাবাকে প্রতিনিয়তই অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয় ।
জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক (বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, হাতের সূক্ষ্ম কাজ), মানসিক (বুদ্ধি, আবেগ, স্মরণশক্তি, চিন্তা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব), সামাজিক ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করাকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয়। আর বিকাশজনিত সমস্যা হলো এমন এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে থাকে এবং শিশুর শরীরের যে কোনো অংশ অথবা সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের নানা ধরনের বিকাশজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, অটিজম সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।
অটিজম কী?
অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার একটি বিস্তৃত রূপ যা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এখানে ‘স্নায়ু’ শব্দটি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুর সম্পর্ক বোঝায়। ‘বিকাশজনিত শব্দটির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে । প্রাকশৈশব কাল থেকে এই সমস্যাটি শুরু হয়, যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতাই এই সমস্যাটির প্রধান বিষয়। এছাড়াও অটিজম রয়েছে এমন শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটা মনে রাখা জরুরি যে, সব অটিস্টিক শিশুই এক রকম নয়। যেমন- অটিজমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কম-বেশি পরিলক্ষিত হয় আবার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। অটিজম স্পেকট্রামে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অটিজম লক্ষ করা যায়। অটিজম স্পেকট্রামকে একটি রংধনুর সাথে তুলনা করা যায়। রংধনুতে যেমন অনেক রং থাকে, অটিজম স্পেকট্রামেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের অটিজম থাকে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম ।
এটিও এক ধরনের অটিজম যা অটিজম স্পেকট্রামে দেখা যায়। এই শিশুদের আচরণগত সমস্যা থাকলেও বুদ্ধিভিত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে কোনো সমস্যা থাকে না। তবে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক এবং শব্দভাণ্ডার পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক আলাপচারিতায় অংশ নিতে এদের সমস্যা হয়। এরা একই ধরনের আচরণ পুনরাবৃত্তি করে থাকে। বিশেষত অন্যের সাথে যোগাযোগের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যেমন-চোখে চোখ রেখে তাকানো, অন্যের মৌখিক অভিব্যক্তি, ইশারা ইঙ্গিত, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ তারা বুঝতে পারে না। এরা কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে, ফলে বাগধারা, প্রবাদ, রসিকতা বা ব্যঙ্গ বুঝতে পারে না। এমন শিশুদের বিকাশ বিলম্বিত হয় না, শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে থাকে, এমনকি বুদ্ধিমত্তাও থাকে সাধারণের চাইতে বেশি। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অ্যাসপার্জার্সের হার দশগুণ বেশি।
এরা যে কোনো বিষয় সঠিক ও সাবলীলভাবে পড়তে শেখে তবে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারে না। সাধারণত অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার অনেক বেশি। খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারে ও অনেক সময় তাদের পছন্দের বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনাও করতে পারে। তবে সে সময় খেয়ালই করে না যে আশেপাশের মানুষেরা সে বিষয়টিতে আগ্রহী কিনা ।
ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রক্রিয়ার সমস্যা এবং শারীরিক নড়াচড়ায় অসুবিধা হবার পাশাপাশি তাদের কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কম থাকে, সময়জ্ঞান কমে যায় এবং মাংসপেশিও শিথিল থাকে, ফলে খেলাধুলার মাধ্যমেও সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সাংগঠনিক ক্ষমতা ও মনোযোগে সমস্যা থাকার কারণে অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা যেতে পারে। নিয়ম নীতি, বিধি, রুটিন ইত্যাদি মেনে চলতে তারা পছন্দ করে। নিয়মের হেরফের ঘটলে তারা মানসিক টানাপোড়নে পড়ে যায় ৷
অটিজম আছে এমন শিশুদের সাধারণ কিছু আচরণ
- চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- ডাকলে সাড়া না দেওয়া
- বিকাশ জনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তনে বাধা দান
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা
- আবেগ প্রকাশে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- সত্যিকার বিপদে ভয় না পাওয়া, অন্যদিকে তেমন বিপজ্জনক নয় এমন অবস্থা বা পরিবেশে অস্বাভাবিক ভয় পাওয়া
- অখাদ্য খাওয়া
- অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না
- কোনো কিছুর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- খাওয়া, ঘুম, মল-মূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- নিজের বা অপরের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবহার
অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো- সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লক্ষণ হিসেবে পরিচিত। অটিজমের কারণে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের উৎসাহ দেখা যায়। এটা জানা জরুরি যে, অটিজমের লক্ষণগুলো স্নায়বিক কারণে হয় এবং একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল নেই ।
ক. সামাজিক লক্ষণসমূহ
অটিজম আছে এমন শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই অন্যের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। জীবনের প্রথম কয়েক মাস তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। তারা অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায় না এবং জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না ।
অটিস্টিক শিশুদের কোনো কিছু শিখতে অনেক সময় লাগে এবং তারা অন্যের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায় না। সাধারণ ইশারা ইঙ্গিত যেমন- মুচকি হাসি, চোখ পিট পিট করা বা মৌখিক অভিব্যক্তি তাদের কাছে কম অর্থপূর্ণ বিষয়। এই সব শিশু যারা ইশারা বুঝতে পারে না তাদের কাছে ‘এদিকে এসো' বাক্যটি সবসময় একই অর্থ বহন করে। অথচ এই বাক্যটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। দেহভঙ্গি ও মৌখিক অভিব্যক্তি না বোঝার কারণে এসব শিশুর কাছে তার সামাজিক জগৎ বোধহীন হয়ে উঠে।
অটিস্টিক শিশুদের উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠার প্রবণতা তাদের সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে বাধা হয়ে দাড়ায়। যখন তারা অপরিচিত ও বাইরের পরিবেশে যায় তখন তারা রেগে যায় বা হতাশ হয়, আবার তাদের কেউ কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এসময় তারা জিনিসপত্র ভাংচুর করতে পারে, অন্যকে আঘাত করতে পারে অথবা নিজের শরীরেও আঘাত করতে পারে ।
খ. যোগাযোগের সমস্যা
যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিছু অটিস্টিক শিশু কখনোই কথা বলতে শেখে না, তারা সারা জীবন নিশ্চুপ থেকে যায়। কোনো কোনো শিশু জন্মের কয়েক মাস পরে বাবলিং বা আধো আধো কথা বলতে শেখে কিন্তু কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে ভাষা শিখতে ৫ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে। অটিজম আছে এমন অনেক শিশুর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তারা শব্দ বিন্যাস করে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না, কেউ কেউ একটি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, কেউ কেউ যে শব্দটি শোনে সেটিই বারবার বলতে থকে। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়া পাখির মতো শব্দটি বার বার এক নাগাড়ে বলতে থাকে, যাকে ইকোলালিয়া বলে । অনেক অটিস্টিক শিশু রয়েছে যাদের ভাষার ক্ষেত্রে খুব সামান্য সমস্যা থাকে। এরা অনেক শব্দ ব্যবহার করে ভালোভাবে কথা বলতে পারে তবে সঠিকভাবে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে না। তারা বাক্যের অর্থের তারতম্য বুঝতে পারেনা। আরেকটি বিষয় হলো শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, কন্ঠস্বর উঠানামার ফলে কথার অর্থের যে ধরনের তারতম্য হয় তা তারা সঠিকভাবে বুঝে না।
গ. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ
অটিজম আছে এমন শিশুরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক এবং প্রায় সবারই পেশি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভালো, কিন্তু অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তাদেরকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে রাখে। এই অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তীব্র থেকে মৃদু হতে পারে। তাদের অনেকেই বার বার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে, অথবা কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে দাড়িয়ে থাকে। তারা অনেক সময় খেলনা গাড়ি বা ট্রেন দিয়ে খেলা করার বদলে এগুলোকে এক লাইনে সাজায়। যদি অসাবধানতাবশত কেউ তাদের এই সাজানো গাড়ি বা ট্রেন নাড়িয়ে ফেলে তবে তারা খুব হতাশ বা বিচলিত হয়ে পড়ে। অটিস্টিক শিশুরা চায় তাদের চারপাশের সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকুক। তারা কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। তাদের দৈনন্দিন রুটিনের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী খাওয়া, গোসল করা, একই রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সামান্যতম হেরফের হলে তারা খুব বিরক্ত হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ তাদের আচরণকে আগে থেকেই যুক্ত করে রাখে যেমন- অটিস্টিক শিশু ফ্যান ঘোরা ও আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ সময় পার করে দেয় ইত্যাদি। তাদের কারো কারো মধ্যে সংখ্যা, চিহ্ন বা বিজ্ঞান বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখা যায় ।
অটিজমের সাথে সম্পর্কিত কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি ও সবল দিক
অটিস্টিক শিশুদের কোনো বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা বা ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর সংখ্যা অতি নগণ্য তবুও এ ধরনের বিশেষ দক্ষতা তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তাদেরকে করে তুলতে পারে অসাধারণ। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মধ্যে এ ধরনের বিশেষ প্ৰতিভা থাকবে। তবে এ বিষয়ে সচেতন থাকলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করা সহজ হবে, শিশুটি সমাজে সমাদৃত হবে এবং তার অন্যান্য দিকের ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে। অটিস্টিক শিশুরা যে বিষয়টির উপর বেশি মনোযোগ দেয় সে দিকেই তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে । দেখা যায় ক্যালেন্ডারের দিকে মনোযোগ আছে এমন শিশুটি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মতারিখ বা বার সঠিকভাবে মনে রাখতে পারে, এভাবে সে একসাথে অনেক তথ্য মনে রাখতে পারে। আবার একটি কঠিন ও কৌশলী কাজকে ছোট ছোট সহজভাগে ভাগ করে এবং সেটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তারা সেই কঠিন ও কৌশলী কাজটি সমাধা করতে পারে।
অটিজম আছে এমন শিশুদের কিছু সবল দিক
- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
- সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির ধারণা, সিকোয়েন্স (ধারাবাহিকতা), প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।
- বিস্তারিত ও মুখস্থ করার মতো বিষয় (গণিত, ট্রেনের সময়সূচি, খেলার স্কোর) মনে রাখতে পারে
- দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ
- বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
- শৈল্পিক দক্ষতা
- অল্প বয়সে লিখিত ভাষা পড়তে পারা (বুঝতে পারুক বা না পারুক)
- বানান মনে রাখা
- সততা
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা
অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার-এর কারণ কী ?
এক কথায় বলতে গেলে অটিজম কেন হয় এখন পর্যন্ত তার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে কারণ অনুসন্ধানের কাজটিও বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন কারণে যে অটিজম হয়ে থাকে এ বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত।বিভিন্ন পর্যায়ে অটিজমের যে জটিল লক্ষণ দেখা যায় তা থেকে বলা যায় যে, একাধিক কারণে অটিজম হতে পারে। জন্মপূর্ব ও জন্মকালীন ও জন্ম পরবর্তী যে কোনো সময়ে জেনেটিক (বংশগতি) এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে অটিজম হতে পারে।
কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই তার অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী কিংবা অটিজমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকই অটিজম নির্ণয় করবেন ।
বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য
অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ
অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিক্ষাদান কার্যক্রম খুবই নিবিড় ও বিশদভাবে হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদের প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষার্থীর আচরণ, বিকাশ, সামাজিক ও একাডেমিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সপ্তাহে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কত সময় ব্যয় করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিতে অটিস্টিক শিশুর শিক্ষাদান সম্ভব নয়, একসাথে বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়। প্রায়োগিক আচরণ বিশ্লেষণ (এপ্লাইড বিহেভিয়ার এনালাইসিস) নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিশুর সবলদিক ও চাহিদার সহায়তার জন্য প্রস্তুতি নিতে অভিভাবকসহ সকল সদস্যের মধ্যে যোগাযোগ থাকা জরুরি এবং ইতিবাচক সফলতার জন্য কার্যকর কৌশল নির্ধারণ, সমন্বয়, সহযোগিতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শুধু শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে দেওয়াই নয়, তাদের মূলধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কার্যকর অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের সফলতার জন্য তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। সেজন্য ছোট ছোট সাফল্যও উল্লেখ করতে হবে। অটিজমের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর গুণাবলি জানা থাকলে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়।
তোমাদের শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক বন্ধুদের তোমরা কীভাবে সহায়তা প্রদান করতে পার অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের ‘সহযোগী বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্বের ধারণা এবং লক্ষ্য অর্জনে একতাবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে অটিস্টিক শিশুরা যথাযথ সহায়তা, সম্মান নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতায় প্রায় সবাই আমরা উপকৃত হব কেননা এদের মধ্যে কেউ আমাদের ভাই, বোন, প্রতিবেশী বা আত্মীয়। অটিজম সংক্রান্ত শিক্ষা বা সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর ভিত্তি করে হবে না, তা সার্বিকভাবে হতে হবে।
শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বুঝতে ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে সহপাঠীদের করণীয়
১. এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়া।
২. শ্রেণিকক্ষের কাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখা।
৩. শ্রেণিকক্ষের জন্য নির্ধারিত রুটিন মেনে চলা ।
৪. সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
৫. শ্রেণি শিক্ষকের পড়ানোর বিষয়টির সারমর্ম বলা এবং মূল বিষয়টি পুনরায় বলা
৬. শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা ।
৭. মৌখিকভাবে অথবা যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরসমূহ লিখিতভাবে প্রকাশে সাহায্য করা
৮. হতাশ হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা।
৯. অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সর্বদা তাকে পুরস্কৃত করা।
১০. শ্রেণিকক্ষের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।
সাধারণত সারাজীবন ধরে অটিজমের লক্ষণগুলো একজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবে যথাযথ সাহায্য, নির্দেশনা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু লক্ষণের উন্নতি হয়। যাদের মাঝে অল্প মাত্রার সমস্যা থাকে তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং তারা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মাঝারি ও বেশি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না এবং নিজের যত্নও নিতে পারে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে অটিস্টিক শিশুরা নানাক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারে।
অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশেও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে, যেমন- প্রয়াস, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সোয়াক, অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে কর্মরত রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারবে।
| কাজ-১ : অটিজমের লক্ষণগুলি লেখ। কাজ—২: শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক শিশুদের সাথে সহপাঠীদের কী করণীয় তা বোর্ডে লেখ । |
Promotion